রাজনীতিবিদ দের সমস্যা টা বুঝুন
শিক্ষা নির্ভর অর্থনীতি
বনাম
শিক্ষা নির্ভর ভোট ব্যাংক
Real সমস্যা হচ্ছে রাজনীতিবিদ দের সমস্যা । আপনি বাজারে যান নতুন বউ কে নিয়ে রিডিং টেবিল কিনবেন বলে। অথচ বাজারে গিয়ে ওয়াশিং মেশিন কিনে আনেন। রিডিং টেবিল টা হয়তো সারা জীবন এ কেনেন এ না। ভোটার দের ও একই অবস্থা।
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
ওই যে মনে মনে চাইলেই তো হবে না দাদা কিনতেও তো হবে রেগুলার। আপনি আপনার প্রেমিকা কে মনে মনে খুব ভালো বসেন কিন্তু আপনার কাজ কর্ম দেখে বোঝা যায় না আপনি তাকে ভালোবাসেন। ভোট ব্যাংক এর ও একই অবস্থা।ভোটার দের ও একই অবস্থা।
বনাম
শিক্ষা নির্ভর ভোট ব্যাংক
Real সমস্যা হচ্ছে রাজনীতিবিদ দের সমস্যা । আপনি বাজারে যান নতুন বউ কে নিয়ে রিডিং টেবিল কিনবেন বলে। অথচ বাজারে গিয়ে ওয়াশিং মেশিন কিনে আনেন। রিডিং টেবিল টা হয়তো সারা জীবন এ কেনেন ও না। ভোটার দের ও একই অবস্থা।
____________________________
প্রশ্ন টা ওঠা স্বাভাবিক। কোন দেশ এর ভোট ব্যাংক শিক্ষা কে এজেন্ডা করে ভোট দিচ্ছে? কোন দেশ এর ভোট ব্যাংক স্বাস্থ্য কে agenda করে ভোট দিচ্ছে? এই প্রশ্ন গুলো অনেক টা গল্পের বই পড়ার জন্য চয়ন করা আর গল্প কে ফিল্ম এ দেখার জন্য চয়ন করা ধরনের সমস্যা। আমরা যেই ধরনের গল্প কে গল্পের বই এ পড়তে চাই সেই একই ধরনের গল্প কি ফিল্ম এ দেখতে চাই? সরকার এর চয়ন এর ক্ষেত্রেও বোধ হচ্ছে তেমন ধরন এর কোন type missmatch হিছে। আমরা যেই ধরনের বিষয় নিয়ে সরকার (যেকোন সরকার) কে দোষ দিই সেই বিষয় গুলোকে সামনে রেখে ভোট কোনদিন দিই না।
কেনো?
100 জন লোক ভোট দিলে 20 জন লোক হয়তো শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কে মাথায় রেখে ভোট দেয় এখন যে কোন দেশে। বাকি 80 জন যখন ভোট দেয় তখন শিক্ষা আর স্বাস্থ্য কে একদম এ মূল্য দিতে চায় না। ফলে কোন ধরনের সরকার এর দায় নেই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার। গনতন্ত্রের চয়ন প্রক্রিয়া গুলো যেই যেই ফ্যাক্টর গুলোকে সামনে রেখে চয়ন করে তাতে "শিক্ষা ফ্যাক্টর"আর "স্বাস্থ্য ফ্যাক্টর" দুটোর ভূমিকা কতোটা??????????????????????????????
শিক্ষা নির্ভর অর্থনীতি বনাম শিক্ষা নির্ভর ভোট ব্যাংক। এই দ্বন্দ্ব শুধু আমাদের দেশে না, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা গভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রে আমরা যা ভোট দেই, আমরা তা-ই পাই। যদি আমরা শিক্ষাকে ভোটে গুরুত্ব না দেই, তাহলে শিক্ষিত সরকার আশা করাও বোকামি।শুধু অর্থনীতি নয়, গণতন্ত্রও শিক্ষা নির্ভর না হলে সেটা কাগজে কলমে থাকবেই, বাস্তবে নয়।
১. শিক্ষা নির্ভর অর্থনীতি
সঞ্জয় নাথ মনে করেন অর্থনীতি তে need lag এবং need lead ধরনের দুটো ফ্যাক্টর রয়েছে যেই বিষয় নিয়ে পলিটিক্স এর উপর সরাসরি প্রভাব পড়ে।peoples need specific memory এবং peoples need specific fear and clearly visible direct immediate threats to daily needs ( uncertainity of immediate needs) যেই যেই বিষয়ের উপরে সরাসরি কাজ করে এবং সারাক্ষণ বেশি স্ট্রং হয়ে মনে বসে থাকে সেই সেই বিষয় গুলো গনতন্ত্র কে সরাসরি চালায়। যেই যেই factor গুলো অনেক দূরে গিয়ে ফল দেয় সেই সেই বিষয় গুলো গনতন্ত্র কে চালায় না কোনদিন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুটি পরিষেবা থেকে immediate needs গুলো তে যাদের জীবন ডিস্টার্ব করে তারা কেবল এই দুটি বিষয় কে সামনে রেখে ভোট দেয়। বাকিদের কোন দায় নেই এই দুটো বিষয় কে সামনে রেখে ভোট দেওয়ার। ফলে সরকার এর ও দায় বোধ তৈরি হয় না।
গণতন্ত্রে আমরা বেশিরভাগ মানুষ এর immediate needs দেখে যা ভোট দেই, আমরা তা ই পাই সারা বছর। যদি আমরা শিক্ষাকে immediate need দেখে ভোটে গুরুত্ব না দেই, তাহলে শিক্ষিত সরকার আশা করাও বোকামি।শুধু অর্থনীতি নয়, গণতন্ত্রও শিক্ষা নির্ভর না হলে সেটা কাগজে কলমে থাকবেই eye wash হয়ে, কিন্তু বাস্তবে নয়।এই ধারণাটি বলছে, একটি দেশের অর্থনীতি যদি শিক্ষিত জনগণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তবে সেই অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই, উদ্ভাবনী এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে দাঁড়ায়। শিক্ষা মানুষকে দক্ষ করে, যুক্তিবাদী করে, এবং প্রগতিশীল করে তোলে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ব্যবসায়, প্রযুক্তিতে, এবং রাষ্ট্রনীতিতে একটা মানসিক পরিণতিবোধ কাজ করে।
২. শিক্ষা নির্ভর ভোট ব্যাংক
এর বিপরীতে, যদি ভোটাররা সচেতন না হয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের ভোটে কোনও প্রাধান্য না থাকে, তাহলে সরকারগুলোরও এগুলো নিয়ে আগ্রহ থাকে না। কারণ ভোট পাওয়ার জন্য যে "জনমত গঠন" করা হয়, তা তৈরি হয় অন্য ফ্যাক্টর দিয়ে—জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, জনপ্রিয়তা, উপহার রাজনীতি, ইত্যাদি দিয়ে।Analogy ছাড়া গাণিতিক মডেল তৈরি টা বেশ কঠিন। কোন একটা সমস্যা কে চিনে নিয়ে যে যতো বেশি relevant well fit analogy তৈরি করতে সক্ষম সে তত ভালো working model তৈরি করতে সক্ষম।Polya plausible reasoning এ খুব গুরুত্ব সহকারে এই বিষয় গুলো বলেছেন।how to solve it??? এর ও অনেক টা অংশ তে ভালো analogy তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে।
৩. গল্পের বই বনাম সিনেমা
সঞ্জয় নাথ এর analogy টা তে বলে আমরা যেই ধরণের গল্প পড়তে পছন্দ করি, সেই ধরণের গল্প হয়তো সিনেমায় দেখতে চাই না।একইভাবে, আমরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে সারা বছর ভাবি ঠিকই, কিন্তু ভোটের বেলায় অন্য কিছু পছন্দ করি হয়তো তাত্ক্ষণিক লাভ, আবেগ, কিংবা পরিচিত রাজনৈতিক মুখ। এই mismatch ই আসল বিপদের জায়গা।
৪. ভোটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ফ্যাক্টরের ভূমিকা
আমাদের দেশে হোক, বা বহু উন্নয়নশীল দেশে
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কতজনের ভোটের প্রাধান্য তালিকায়?
সম্ভবত ১৫–২০% মানুষ এগুলো গুরুত্ব দেয়। বাকি ৮০–৮৫% হয়তো শুধু ভোট দেয়
কে পরিচিত,
কে গতবার রাস্তা বানিয়েছে,
কে কতো উপহার দিয়েছে,
কে নিজের জাত/ধর্ম/ভাষার লোক,
ইত্যাদি বিষয় দেখে।
ফলে সরকারও ভাবে “যেহেতু মানুষ এগুলোর ওপর ভোট দেয় না, তাহলে আমিও এগুলোর পেছনে বাজেট নষ্ট করবো না”।
৫. তাহলে সমাধান কোথায়?
ভোটারদের সচেতনতা বাড়ানো জরুরি, যেন তারা বুঝতে পারেন শিক্ষা স্বাস্থ্য ছাড়াও কিছুই টেকসই নয়।মিডিয়া, সামাজিক আন্দোলন, তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।শিক্ষিত সমাজকে শুধু অভিযোগ না করে, স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হতে হবে।শিক্ষাকে ভোটের এজেন্ডা বানাতে হবে—সোশ্যাল মিডিয়ায়, লোকাল লেভেলে, আলোচনায়। ঐযে বলছি গণতন্ত্রে আমরা যা ভোট দেই, আমরা তা-ই পাই। যদি আমরা শিক্ষাকে ভোটে গুরুত্ব না দেই, তাহলে শিক্ষিত সরকার আশা করাও বোকামি।শুধু অর্থনীতি নয়, গণতন্ত্রও শিক্ষা নির্ভর না হলে সেটা কাগজে কলমে থাকবেই, বাস্তবে নয়।
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Real সমস্যা হচ্ছে রাজনীতিবিদ দের সমস্যা । আপনি বাজারে যান নতুন বউ কে নিয়ে রিডিং টেবিল কিনবেন বলে। অথচ বাজারে গিয়ে ওয়াশিং মেশিন কিনে আনেন। রিডিং টেবিল টা হয়তো সারা জীবন এ কেনেন এ না। ভোটার দের ও একই অবস্থা। তারা যা দাবি করে কখনও কখনও মিছিল করে সেই দাবি কে সামনে 5রেখে ভোট দেয় না কোনদিন।😆😆😗😗😆😆 80%জনতা মোমো খেতে পছন্দ করে। কফি হাউস চায় না। তারা কফি হাউস এ যায় ও না। কফি হাউস এ গিয়ে আনন্দ ও পায় না।রাজনীতিবিদ হচ্ছে একজন কাপড় এর দোকান দার। সে দেখছে তার সারাদিনে অনেক কিছু করে আলো জ্বালিয়ে ac চালিয়ে যত লাভ হচ্ছে সেই আলোয় দাড়িয়ে সামনের মোমো ওয়ালা 3 গুল লাভ করছে। ফলে কাপড় বিক্রি ছেড়ে সে মোমো বিক্রি করছে এখন। রাজনীতিবিদ দের সমস্যা টা অনেক টা এমন analogy র সাথে মিলিয়ে দেখাও দরকার।
তারা এগুলো না করলে 80% লোক ভোট দেয় না। আর 20%লোক শিক্ষা ভালো করলে অথবা স্বাস্থ্য ভালো করলে সেই দেখে যারা সম্মান করে রাজনীতি বিদ দের
সেই 20% ও ভোট দেওয়ার সময় এই ফ্যাক্টর গুলো দেখে ভোট দেয় না ।আপনিও হয়তো শিক্ষা স্বাস্থ্য ফ্যাক্টর দেখে ভোট দেওয়ার সময় ভোট টা দেন না।আমিও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে ভোট দিই না । আমিও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখে ভোট দিই না। আপনিও হয়তো দেন না।আমরা বাজেট দেখি, ইনকাম ট্যাক্স এর ছাড় দেখি, জিনিস এর দাম দেখি,(অনেকেই public transport এর ভাড়া নিয়েও চিন্তিত নয়)এমনিতেই সরকারি স্কুলে আমার চেনা কেউ পড়ে না। কোন চেনা আত্মীয় সরকারি হাসপাতাল ও যায় না।আমরা নেতার মুখ দেখি ভোট দেওয়ার আগে। আমরা পাড়ায় মন্দির মসজিদ গির্জার দাপট এ বিরক্ত কিনা সেইটা দেখি ভোট দেওয়ার আগে। আমরা দেখি কোন দলের পুলিশ আমাকে কবে ডিস্টার্ব করেছে অথবা গাড়ি পার্ক করতে দেয় নি। রাগ ভুলতে পারিনি। আমরা এগুলো দেখি ভোট দেওয়ার আগে। আমরা পাড়ার জল এর সমস্যা দেখি। পাড়া তে security সমস্যা দেখি।সত্যিই কি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার রেকর্ড দেখি ভোট দেওয়ার আগে??? সত্যিই কি সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রেকর্ড দেখি ভোট দেওয়ার আগে??? এমনিতেও সেগুলো ভালো হলে কলকাতায় হয়েছে আমার গ্রামে কি ভালো হয়েছে??? Immediate 1 বছরে আমার কি ব্যক্তিগত লাভ হয়েছে তাতে? কি যায় আসে আমার তাতে immediately???????????????????
“আমরা সরকার বদলাই, কিন্তু সরকার বদলায় না—কারণ আমরা নিজের ইচ্ছে বদলাই না।”আমরা যেন আমাদের ইচ্ছের সেই বদলটা শুরু করতে পারি তবেই রাজনীতিবিদ দেরও বাধ্য করতে পারি "মোমো না বিক্রি করে, কাপড়" বিক্রি করতে।এইটা একটা সম্মিলিত মনস্তত্ত্ব (collective psychology) যেখানে রাজনীতি, জনগণ, এবং নৈতিক এজেন্ডা—সব এক অদ্ভুত চক্রে বন্দি।
রাজনীতিবিদ = মোমো বিক্রেতা (vs কাপড় ব্যবসায়ী)
এই analogy টা ও হয়তো চলতে পারে polya model অনুযায়ী।রাজনীতিবিদরা যখন দেখে যে আলো, এসি, বড় চিন্তা করে শিক্ষানীতি বানিয়ে, স্কুল চালিয়ে, চিকিৎসা উন্নত করে লাভ নেই কারণ সেই ফ্যাক্টর গুলো যতই ভালো করুন যতই খরচ করুন সেই ফ্যাক্টর দেখে 80% মানুষ ভোট দেয় না এই কাজগুলো দেখে তখন তারা “মোমো” বিক্রি শুরু করে। অর্থাৎ
ছোটো মিটিং,
হিন্দু মুসলিম তাস,
খিচুড়ি রান্না,
বাইকে করে ঘোরা,
জনপ্রিয় কিছু শ্লোগান,
ফেসবুক পোস্ট,
এইগুলোতেই ফোকাস দেয়। কারণ ভোট তো এর জন্যই আসে।
ভোটার মানসিকতা
আমি তো ব্যবহারই করি না ফলে আমি সেই বিষয় কে সামনে রেখে ভোট অবশ্যই দেবো না। তাতে আমাকে যা ইচ্ছে বলো। গালি দাও। পাত্তা দেবো না। আমি সরাসরি immediately যা চাই সরকার এর কাছে সেই agenda তেই ভোট দিই।
"আমার কেউ তো সরকারি স্কুলে পড়ে না"
"আমি নিজেও সরকারি স্কুলের কোন সুবিধে পাই না"
"আমি নিজেও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন সুবিধে পাই না"
"আমার আত্মীয় তো প্রাইভেট ক্লিনিকে যায়"
"আমার গ্রামে কি হয়েছে তা নিয়ে আমার বাস্তবিক আগ্রহ কম"
"আমি নেতার ব্যবহার, পুলিশ বা পার্টির attitude দেখে ভোট দিই"
ফলে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নিয়ে ভোট দেওয়ার কোনো বাস্তব প্রেরণা আমরা পাই না।
এই সমস্যা তাহলে কার?
এই জায়গায় এসে রাজনীতিবিদদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ তারা মোমো বিক্রি করে যে বাজারে চাহিদা আছে।
সমস্যা সিস্টেমিক
এটা
1 একটানা অবহেলা,
2 অনভ্যাস,
3 অবিশ্বাস,
এবং "নিজের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব নেই"এই মানসিকতা থেকে গড়ে উঠেছে।
সমাধান কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়
১. শিক্ষিত অংশের মনোভাব বদলানো দরকার
যারা সরকারি স্কুলে যায় না, তবু বোঝে রাষ্ট্রব্যবস্থা কি।
২. নতুন ভোটারদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে শেখানো দরকার “তোমার সন্তান ভবিষ্যতে কী পাবে সেই প্রশ্নে তুমি ভোট দিচ্ছো কি না” এই বোধ তৈরি করতে হবে।
৩. মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক আলোচনায় শিক্ষাকে "গর্বের জায়গা" বানাতে হবে যেমন সিনেমা বানাই যুদ্ধ নিয়ে, তেমন শিক্ষার উন্নতি নিয়ে বানালে?“আমরা সরকার বদলাই, কিন্তু সরকার বদলায় না—কারণ আমরা নিজের ইচ্ছে বদলাই না।”আমরা যেন আমাদের ইচ্ছের সেই বদলটা শুরু করতে পারি তবেই রাজনীতিবিদদেরও বাধ্য করতে পারি "মোমো না, কাপড়" বিক্রি করতে।
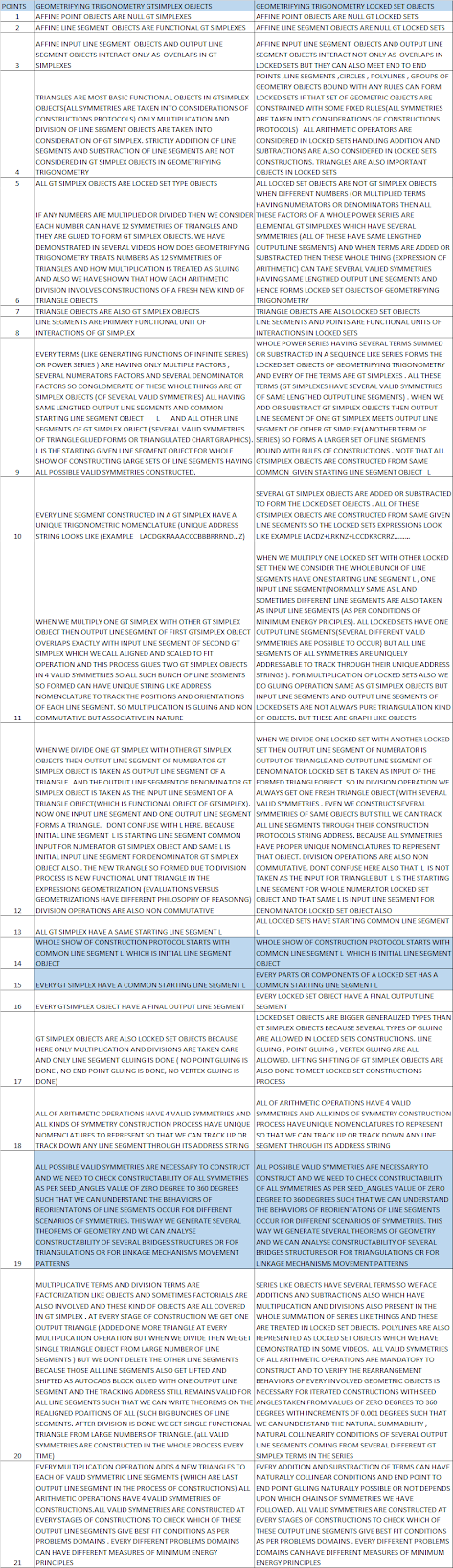
Comments
Post a Comment